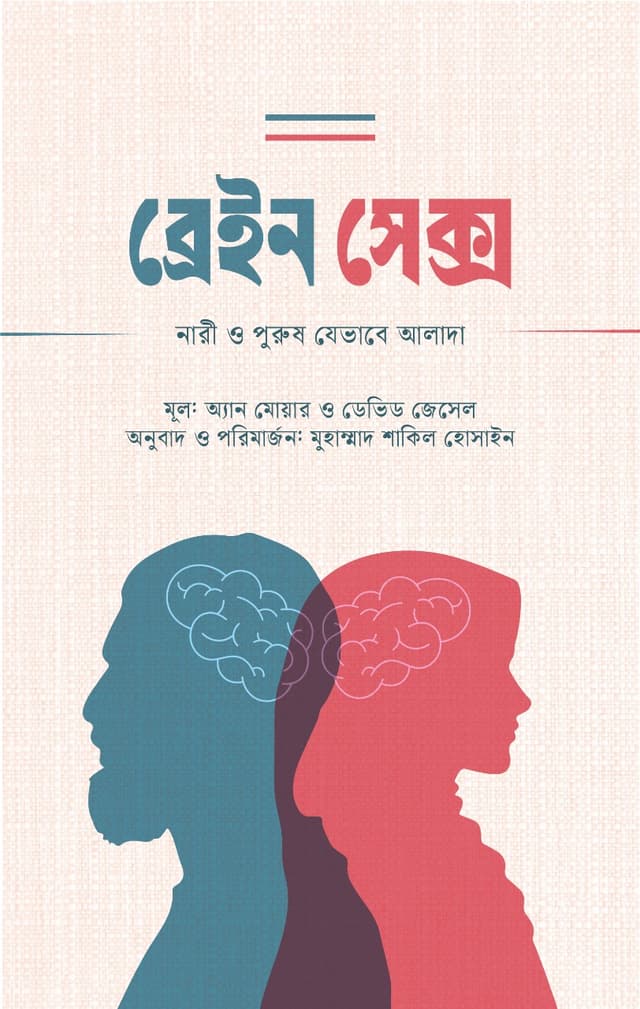
by অ্যান মোয়ার, ডেভিড জেসেল
নারী ও পুরুষ আলাদা সত্তা নয়—তারা মূলত একই ধরনের, সর্বাংশে এক ও অভিন্ন—এই কথা বর্তমানে প্রায় সবাই জানে। নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা বলা হয়, তা আসলে প্রকৃতিগত নয়; বরং সমাজ-নির্মিত একটি ধারণা—social construct। প্রশ্ন আসে, কোন সমাজ? সেই সমাজ, যা যুগের পর যুগ পুরুষশাসিত, পিতৃতান্ত্রিক। যে সমাজ নারীদের অধীনস্ত রাখতে চায়।
ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, এই সমাজব্যবস্থাই নানা পুরাণকথা (myth) আর গল্পের মাধ্যমে মানুষের মনে এই বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছে, যা নারী-পুরুষের পার্থক্য স্বাভাবিক, এমনকি অপরিহার্য। তারা সত্তাগতভাবে একে অন্যের থেকে আলাদা। এই মৌলিক স্বীকৃতিটুকুই সমাজের প্রতিটি স্তরে জন্ম দিয়েছে লিঙ্গ-বৈষম্য, লিঙ্গ-বিভাজন ও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস। সমাজ-ই নির্ধারণ করে দেবে—নারী কেমন পোশাক পরবে, কোথায় যাবে, কী ধরনের আচরণ করবে, কোন দায়িত্ব পালন করবে এবং কোন কাজ থেকে বিরত থাকবে ইত্যাদি সবকিছু। এই অসংখ্য বিধিনিষেধের মূল শেকড় হলো সেই বিশ্বাস—নারী আর পুরুষ একে অন্যের থেকে আলাদা।
কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির তৈরী করা লক্ষ্মণরেখা থেকে বেরিয়ে এসে ভাবলে দেখা যাবে—এই বিশ্বাসের পক্ষে কোনো অটল ভিত্তি নেই। বরং আছে সামাজিক অভ্যাস ও সংস্কার। এ কারণে প্রায়ই শোনা যায় বিখ্যাত সেই লাইন—'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, নারী হয়'। অর্থাৎ সমাজই 'নারী' তৈরি করে। তাই, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যে চিন্তার বাঁধন গড়ে তুলেছে ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করেছে, সেখান থেকে মুক্তি পেলেই নারীরা প্রকৃত মুক্তি পাবে—এমনটাই বলতে শোনা যায়।
আর তাই নারীমুক্তির প্রসঙ্গ উঠলে এটা জোর দিয়ে অবশ্যই বলা হবে যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একসময় এই ধারণা ছিলো কেবল কিছু মানুষের সমস্বর, ঐক্যমত্য; কিন্তু আধুনিক কালে এটি হয়ে উঠেছে এক বৃহৎ সভ্যতার (পশ্চিমা সভ্যতার) সাংস্কৃতিক পাটাতন ও দার্শনিক কেন্দ্রবিন্দু। এখন যে কেউ যদি বলে—নারী ও পুরুষ ভিন্ন—তা আর কেবল মতবিরোধ নয়, বরং গুরুতর অপরাধ, কারো কাছে ঈশ্বরনিন্দার সমান। বিপরীত মতামত, যতই প্রমাণসমর্থিত বা যুক্তিসম্মত হোক না কেন, তা অবিলম্বে বাতিল বলে গণ্য করা হয়।
কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায়—এটা কি সত্যিই পুরুষদের বানানো এমন এক বাঁধন, যা নারীদের পদতলে রাখার জন্য পরিকল্পিত? নাকি বাস্তবিক অর্থেই নারী ও পুরুষ একেবারে অভিন্ন? তারা কি কেবল শরীরের গড়ন ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আলাদা নয়?
এ প্রশ্নের একদিকে গভীর দার্শনিক দিক রয়েছে—যা নিয়ে হাজার বছর ধরে দার্শনিকরা তর্ক-বিতর্ক করে আসছেন। নির্দিষ্ট কোনো সর্বসম্মত উত্তর মেলেনি। অন্যদিকে, এই প্রশ্নের সামাজিক তাৎপর্যও অপরিসীম। কারণ নারী-পুরুষ ভিন্ন—এমন ধারণার উপর দাঁড়িয়েই আছে প্রথাগত সামাজিক কাঠামো, পারিবারিক ভূমিকা, সামাজিক মর্যাদা ও দায়িত্ববন্টন। বলা যায়, এ প্রশ্নটাই আধুনিক নারীবাদের প্রাণকেন্দ্র; এর সঠিক উত্তরের ওপর নির্ভর করছে বহু সামাজিক ধারণা ও মূল্যবোধের ভবিষ্যৎ।
ব্রিটিশ লেখকদ্বয় অ্যান মোয়ার ও ডেভিড জেসেল তাদের আলোচিত গ্রন্থ Brain Sex-এ নারী ও পুরুষের মস্তিষ্ক, আচরণ ও প্রবণতার প্রাকৃতিক পার্থক্য বিষয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। বইটি এই বিষয়ে এক ধরণের ক্লাসিক হিসেবে স্বীকৃত। অত্র গ্রন্থটি সে বইয়ের-ই বাংলা অনুবাদ। আশা করি এটি কৌতূহলী পাঠকের জিজ্ঞাসা কিছুটা হলেও মেটাতে পারবে, এবং নারী-পুরুষ সমতা ও পার্থক্য নিয়ে চলমান বিতর্কে নতুন দৃষ্টিকোণ যোগ করবে।
| প্রকাশক | ওয়াটারমার্ক পাবলিকেশন |
| লেখক | অ্যান মোয়ার, ডেভিড জেসেল |
| অনুবাদক | মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন |
| বিষয় | নারী-পুরুষের পার্থক্য, নারীবাদ |
| ISBN | N/A |
| পৃষ্ঠা | 176 |
| বাঁধাই | পেপার ব্যাক |